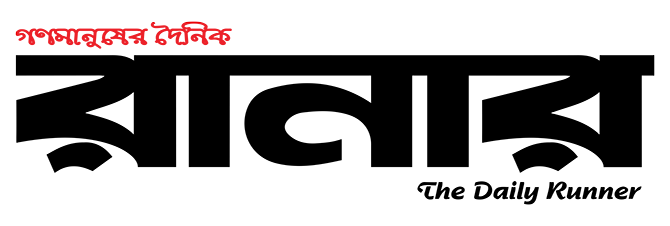জীর্ণ কুটিরের ছবিটি রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার উপজাতি পল্লি আদাড়পাড়া থেকে তোলা। শিকারে বের হওয়ার আগে তীর-ধনুক হাতে সাঁওতাল নারী-পুরুষ।
জীবনমানের সব সূচকেই একদম পিছিয়ে রয়েছে বরেন্দ্র অঞ্চল রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলায় বসবাসকারী কমবেশি ১৫টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, স্যানিটেশনসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে সুবিধাবঞ্চিত এখানকার সাঁওতাল, ওরাওঁ, মাহালি, সিংহ, ভূমিজ, রবিদাস ও অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষেরা। কৃষি কাজে নিম্ন মজুরি এসব উপজাতিদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা। শিক্ষার হারেও মূলধারার জনগোষ্ঠীর চেয়ে অনেক পেছনে পড়ে আছে। ভাষাগত সমস্যা ও বসতি থেকে দূরবর্তী স্কুল- এসব ক্ষুদ্র-জাতিগোষ্ঠীগুলোর শিশুদের লেখাপড়ার ব্যাপারে প্রধান অন্তরায়। এ ছাড়া উপজাতিদের পাড়াগুলোয় সুপেয় পানির সংকট চলে বছরজুড়ে।
গোদগাড়ী উপজেলায় অন্যান্য উপজাতিদের চেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাঁওতালেরা শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে। ভাষাগত সমস্যার কারণে সাঁওতাল শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষার স্তর পেরোনোর আগেই ঝরে পড়ছে। বাংলা ভাষায় দুর্বলতা থাকায় প্রাথমিকের গণ্ডি পেরোতে পারছে না। দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যা চলতে থাকায় জাতিগোষ্ঠীটির হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত।
গোদাগাড়ীর উপজাতিদের প্রায় সবাই কৃষি শ্রমিক। কৃষি মজুরি তাদের জীবিকার প্রধান উৎস। ধান চাষাবাদে অন্যের জমিতে শ্রম বিক্রি করেন প্রত্যেক উপজাতি পরিবারের নারী-পুরুষ। ক্ষেত মজুর হিসেবে মাঠ প্রস্তুত, জমিতে চারা রোপণ, সার দেওয়া, আগাছা পরিষ্কারসহ ধান চাষের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য কাজ করেন। জমি বর্গা নিয়ে চাষাবাদও করেন এখানকার উপজাতিদের কেউ কেউ। তবে সংখ্যায় সেটি একেবারেই নগণ্য।
আলপচারিতায় জানা গেছে, এক্ষেত্রে ধান আবাদের ব্যয় জোগাতে হিমশিম দশা হয়। ফলে প্রয়োজনীয় পুঁজির জন্য এনজিও’র কাছ থেকে ঋণগ্রহণ করেন। আর এতে ঋণের সুদ দিতে গিয়ে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ফলে লাভের দেখা বরাবরই কম পেয়ে থাকেন। আবার কোনো কোনো বার ফসলের কাঙ্ক্ষিত দাম না পেয়ে লোকসান গুনতে হয়। এ ছাড়া প্রান্তিক চাষি হিসেবে মূলধারার জনগোষ্ঠীর অন্যদের মতো প্রণোদনা হিসেবে সার, বীজ ও কীটনাশকসহ অন্যান্য সুবিধাগুলো পান না।
গোদগাড়ি উপজেলার পাকড়ী ইউনিয়নের জাওয়াই পাড়ার বাসিন্দা উদয় চন্দ্র শীল জানান, অল্প কিছু জমি বর্গা নিয়ে ধান আবাদ করেন। কিন্তু ফি বছর ন্যায্য দাম না পেয়ে লোকশানের মুখে পড়েন।
সরেজমিন দেখা যায়, দিগন্ত বিস্তৃত ফসলের মাঠের পাশে সারি সারি মাটির ঘর বিছিয়ে থাকা একটি গ্রাম জাওয়াই পাড়া। এখানকার অধিবাসীরা মাহাতো, শীল ও সিংহ জাতিগোষ্ঠী। অপরের ক্ষেতে কৃষি শ্রমিকের কাজের পাশাপাশি কেউ কেউ জমি লিজ ও বর্গা নিয়ে ধান আবাদ করেন। এ ছাড়া নাপিতের কাজ ও বাড়িতে গরু, ছাগল ও হাঁস-মুরগি পালন করেন প্রায় সবাই।
অন্য উপজাতিদের থেকে জাওয়াই পাড়ায় বসবাসরত তিনটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ায় বেশ এগিয়ে। এখানকার প্রবীণ নারী চঞ্চলা রানি (৭৪) ১৯৭৩ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন। কিন্তু এরপর আর লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারেননি। আক্ষেপ করে এই নারী বলেন, কুসংস্কারের কারণে উচ্চশিক্ষা বঞ্চিত হয়েছেন। তার বাবা-মা বাড়ি থেকে অনেক দূরে অন্য কোথাও গিয়ে লেখাপড়া করতে দিতে চাননি। ফলে ইচ্ছা থাকলেও সাধ পূরণ হয়নি। তিনি বলেন, এখনো এই ভেবে আফসোস করি যে, যদি আরো অনেক দূর লেখাপড়া করতে পারতাম, তাহলে সরকারি কোনো চাকরি করে উন্নত জীবনযাপনের সুযোগ পেতাম। পরিবারে আর্থিক সচ্ছলতা ফিরতো।
জানা গেল, এই গ্রামটির ছেলেমেয়েদের অনেকেই রাজশাহী শহরে মেসে-হোস্টেলে থেকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে। গ্রাম থেকে প্রতিদিন রাজশাহী শহরে গিয়ে ক্লাসে অংশ নেন অনেকে। এক্ষেত্রে পড়াশোনার খরচ যোগাতে বাবা-মায়েদের মতো কৃষিকাজের পাশাপাশি টিউশনি করেন তারা।
জাওয়াই পাড়ার বাসিন্দা প্রতিমা রানি বলেন, তাদের জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার হার অন্যদের তুলনায় বেশি। ছেলেদের মতো তাদের মেয়েরাও অনেকে লেখাপড়া শিখছে। তবে মেয়েদের মধ্যে ‘ব্রেক অব স্টাডি’র ( অধ্যয়ন বিরতি) মত ঘটনা ঘটছে বেশি। বিশেষ করে বিয়ে হয়ে যাওয়ার কারণে অনেকে লেখাপড়া বেশি দূর এগিয়ে নিতে পারছে না। আবার অনেকে বিয়ের পর বিরতি দিয়ে ফের লেখাপড়ায় ফিরছে। ফলে উচ্চ শিক্ষা শেষ করতে অনেকের দীর্ঘ সময় লাগছে। তিনি জানান, এবার এইচএসসি পরীক্ষা দেবেন। বিয়ে হয়ে যাওয়ার কারণে একবছর মত পড়াশোনা বন্ধ ছিল। এরপর পুনরায় শুরু করেছেন।
গোদাগাড়ী উপজেলার পাকড়ী ইউনিয়নের জ্ওাইপাড়া ও ঝিনা ঝালপুকুর, রিশিকুল ইউনিয়নের মান্ডইল রামদাসপাড়া, তালাই কুন্দলিয়া, মাটিকাটা ইউনিয়নের চৌদুয়ার, আদাড়পাড়া এবং দেওপাড়া ইউনিয়নের কুড়াপুড়া ও জীওলমারী ঘুরে দেখা গেছে, এখানকার উপজাতি জনগোষ্ঠীর বসতিগুলোর অবস্থা একদমই জরাজীর্ণ। বহুসংখ্যক মাটির ঘরের দেয়াল থেকে ঝুরঝুরে মাটি খসে পড়ছে। টিনের চালায় মরিচা পড়ে বেহাল দশা। পাড়ার ভেতরে মাটির রাস্তা বর্ষা কাদায় ‘প্যাচপেচে’ অবস্থা।
মান্ডইল রামদাসপাড়ার বাসিন্দারা জানান, বছরভর সুপেয় পানির সংকট তাদের। এলাকায় কোনো টিউবয়েল না থাকায় বরেন্দ্র প্রকল্পের পানি তাদের একমাত্র ভরসা। ভূগর্ভেও পানির স্তর বহুবছর ধরে নিচে নেমে থাকায় টিউবওয়েল দিয়ে পানি ওঠে না।
ওই পাড়াটির বাসিন্দা রাজশাহী কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের স্নাতক শ্রেণির শিক্ষার্থী অপু রাম দাস জানান, বরেন্দ্র প্রকল্প থেকে সরবরাহ পানি প্রায়শই থাকে কালচে ও ময়লা মিশ্রিত। সেই পানি পানের উপযোগী থাকে না। এই এলাকায় কয়েকটি সাবমারসিবল পাম্প আছে। শুষ্ক মৌসুমে যখন বরেন্দ্র প্রকল্প থেকে পানের অনুপযোগী ময়লা পানি সরবরাহ হয় করা; তখন স্বল্প সংখ্যক সাবমারসিবল দিয়ে চাহিদা পূরণ হয় না।
আলাপচারিতায় জানা গেল, সরকারি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা যেমন বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধী ভাতাসহ অন্যান্য ভাতা প্রাপ্তি যে- তাদের জনগোষ্ঠীরও অধিকার সেটি জানতেন না। রামদাসপাড়ার বাসিন্দা শ্যামলী রানি জানান, তাদের পাড়ায় রিইব’র (রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ) গণ-গবেষণা দল গঠনের আগে এসব বিষয়ে ছিলেন তারা অজ্ঞ। সংস্থাটির কার্যক্রম শুরুর পর তারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে জানতে পেরে সচেতন হয়েছেন।
স্থানীয় আরেক বাসিন্দা সুবর্ণা রানী বলেন, আগে ইউনিয়ন পরিষদে যেতে সাহস পেতাম না। এখন পরিষদে গিয়ে নিজেদের বিভিন্ন সমস্যা-সংকটের কথা চেয়ারম্যান-মেম্বারদের কাছে তুলে ধরি। সরকারি বিভিন্ন ভাতা ও সেবা-সুবিধার জন্য ইউনিয়ন পরিষদে আবেদন করি। এ সব কিছুই সম্ভব হয়েছে গণগবেষণা দলের বৈঠকে অব্যাহত আলোচনা ও তথ্য আবেদনের ফলে।
তিনি আরো জানান, রিইব তাদের তথ্য অধিকার আইনের ওপর প্রশিক্ষণ দিয়েছে। উঠান বৈঠক ও কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে তাদের মতো পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মানুষদের সচেতন করে তুলেছে। আইনটি প্রয়োগ করে এখন তারা সরকারিভাবে তাদের প্রাপ্য সেবা-সুবিধা সম্পর্কে জানতে পারছেন। আর এভাবে রিইব তাদের চোখ খুলে দিয়েছে।
গ্রামের সবচেয়ে প্রবীণ বাসিন্দা ও পাড়ার মোড়ল শ্যামপদ রামদাস জানান, রিইব’র গণ-গবেষণা দলের সভায় এখন আমরা আমাদের সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে সবাই মিলে সমাধান করি। এক্ষেত্রে সমস্যা মেটাতে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করতে রিইব তাদের মুষ্ঠির চাল সংগ্রহ শিখিয়েছে। প্রত্যেক ঘর থেকে প্রতি সপ্তাহে মুষ্ঠির চাল সংগ্রহ করা হয়। চাল বিক্রির টাকা মন্দিরের উন্নয়ন, পূজা-অর্চণাসহ অন্যান্য সমস্যা সমাধানে ব্যয় করা হয়।
তিনি আরো জানান, রিইব’র কর্মীরা সরকারি দপ্তরের সাথে যোগায্গো করিয়ে দেওয়ায় দর্জি প্রশিক্ষণ নিয়ে বেশ কয়েকজন স্বাবলম্বী হয়েছেন। ৫ জন সেলাই মেশিনও পেয়েছেন। অনেক নারী বাড়ীতে বসে নানা ধরনের অর্থনৈতিক কাজে যুক্ত হয়েছেন। আর এভাবে নারীরাও যে পরিবারের অর্থনীতির অংশ হতে পারেন সেটি তারা আগে জানতেন না।
গোদাগাড়ী উপজেলার পাকড়ী, দেওপাড়া ও মাটিকাটা ইউনিয়নে বসবাসরত উপজাতিদের গ্রাম ঘুরে আলাপচারিতায় জানা যায়, বরেন্দ্র এলাকায় মাঠের কাজে মজুরির হার দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক কম। এক্ষেত্রে উপজাতি নারীরা মজুরি বৈষম্যের শিকার। পুরুষদের তুলনায় নারী কৃষি শ্রমিকদের দিনমজুরি কম দেওয়া হয়। পুরুষেরা দিন ৩৫০ টাকা ও নারীরা ৩০০ টাকা বা তারচেয়ে কম মজুরি পান।
দেওপাড়া ইউনিয়নের কুড়াপাড়া গ্রামের বাসিন্দা পারুল রানিসহ আরো বেশ কয়েকজন নারীর সাথে কথা বলে জানা গেছে, ধানচাষে কৃষি শ্রমিকের কাজটি মূলত মৌসুমি। আবাদ মৌসুম শেষে তারা বেকার হয়ে হয়ে পড়েন। সেই সময় অন্নকষ্টে ভোগেন। এ ছাড়া স্বল্প মজুরির টাকায় জীবনমানের উন্নয়ন দূরে থাক; দিনকার খোরাকি জোগানো কঠিন হয়ে পড়ে।
মাঠে একই কাজ করে পুরুষদের তুলনায় কম মজুরির ব্যাপারে এখানকার নারীদের ভাষ্য, পুরুষদের শক্তি ও সামর্থ্য তাদের তুলনায় বেশি। যার কারণে পুরুষদের চেয়ে কম মজুরি তারা মেনে নিয়েছে।
এই গ্রামের নারীরা জানান, রিইব’র কার্যক্রম শুরুর আগে প্রতিবন্ধী ভাতা বা সনাক্তকরণ, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতার মতো সরকারি সুযোগ-সুবিধাগুলো যে- আমাদের প্রাপ্য তা জানা ছিল না। রিইব’র প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায়গুলোয় তথ্য অধিকার ও মানবাধিকারের বিভিন্ন বিষয়গুলো সম্পর্কে জেনেছি। যা আমাদের নায্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছে।
এই গ্রামের নারীরা আরো জানান, তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে আবেদন করে সরকারের আশ্রয়ন প্রকল্পের অধীনে খাসজমিসহ ঘর প্রাপ্তির বিষয়ে জানতে পেরেছিলেন। এরপর দুটি গ্রামের ৪০টি পরিবার আবেদন করেছে। ইতোপূর্বে ২৫টি পরিবার এই প্রকল্পের আওতায় জমিসহ ঘর পেয়েছে।
জানা গেছে, অমৌসুমে অর্থাৎ ধানের চাষাবাদ যখন থাকে না; তখন সাঁওতালসহ অন্যান্য উপজাতির পুরুষেরা শিকারে বের হন। জঙ্গল এলাকায় ঘুরে ঘুরে শিকারের সন্ধান করেন। তীর-ধনুক ও বর্শা দিয়ে বন বেড়াল, বেজি, কাঠবেড়ালিসহ অন্যান্য ছোটখাটো বন্য জন্তু শিকার করে আনেন।
কুড়াপাড়া গ্রামের সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তি রূপলাল হেমব্রম, বয়স এখন ৮০ ঊর্ধ্ব। তিনি জানান, তাদের এই এলাকাটি এক সময় জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। বাঘের মতো ভয়ংকর বন্য জন্তুর বিচরণ ছিল। জঙ্গল সাফ করে ও উঁচু-নিচু জমি কেটে সমান করে এই ভূমি তাদের পূর্বপুরুষেরা কৃষি কাজের উপযোগী করে তুলেছেন। তাদের হাতে এই বরেন্দ্রভূমি চাষ কাজ ও বসবাসের উপযোগী হলেও তাদের বেশির ভাগই ভূমিহীন। মাথা গোঁজার জন্য এক চিলতে জমি হয়ত আছে; কিন্তু চাষের জমি বলতে গেলে তাদের কারোরই নেই।
জানা গেছে, গোদগাড়ী উপজেলায় প্রায় ৬০ হাজার বিভিন্ন উপজাতি পরিবারের বসবাস। অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকের মত শিক্ষার ক্ষেত্রেও তারা অনেক বেশি অনগ্রসর। বিশেষ করে এখানকার সাঁওতাল জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার হার সবচেয়ে কম। এক্ষেত্রে ভাষাগত সংকট সবচেয়ে বড় সমস্যা।
কাদমা ফুৃলবাড়ী গ্রামের বাসিন্দা সিলভিয়া শিল্পী মুর্মু জানান, উচ্চ মাধ্যমিকের পাসের পর অর্থনৈতিক সংকটের কারণে লেখাপড়া বেশিদূর চালিয়ে নিতে পারেননি। তিনি বলেন, বাংলা ভাষা না জানার কারণে তাদের জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার হার অনেক কম। তাদের অনেকে বাংলা বলতে জানেন; কিন্তু শিক্ষিতরা ছাড়া বাংলা বর্ণমালায় পড়তে ও লিখতে জানেনা কেউ। অন্যান্য উপজাতি গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে বাংলায় কথা বললেও সাঁওতালদের মধ্যে সেটির প্রচলন কম।
তিনি জানান, বাবা-মায়েদের বাংলা বর্ণমালার জ্ঞান-পরিচয় না থাকায় শিশুরা সেটি বাড়িতে শিখতে পারে না। আবার স্কুলে গিয়ে বাংলা ভাষায় পাঠদান বুঝতে পারে না। যার কারণে লেখাপড়া বেশিদূর এগোয় না। প্রাথমিক স্তরেই ঝরে পড়ে।
সিলভিয়া শিল্পী মুর্মু আরো জানান, এখানকার উপজাতিদের বেশিরভাগ গ্রামগুলো থেকে প্রাইমারি স্কুলগুলো অনেক দূরে। ছোট্ট শিশুদের পক্ষে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে স্কুলে যাওয়া হয়ে ওঠে না। এটিও প্রাথমিক স্তরেই শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে পড়ার আরো একটি কারণ।
পাকড়ী ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য (ইউপি মেম্বার) নূরুল ইসলাম বকুল জানান, অনেক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এই ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে প্রাক-প্রাথমিক স্কুল চালু করেছে। সেখানে উপজাতিদের মধ্যে যারা শিক্ষিত তারা স্কুলগুলোয় শিক্ষকতা করছেন। এতে ধীরে অবস্থার উন্নতি হয়ে পরিস্থিতি বদলাচ্ছে।
তিনি জানান, উপজাতিদের শিক্ষিত অংশের যারা স্কুলগুলোর শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন; তারা তাদের জাতিগোষ্ঠীর শিশুদের বাংলা শেখাচ্ছেন। এতে উপজাতিদের ছোট ছেলেমেয়েরা বাংলায় লিখতে ও পড়তে শিখছে। আর এভাবে ভাষাগত সংকটের কারণে শিক্ষাগ্রহণের যে বাধা ছিল সেটি আস্তে আস্তে কমে আসবে।
গোদাগাড়ী উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মোহা. আব্দুল মানিক জানান, এই উপজেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলো সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সহায়তা পেয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে পরিবার প্রধানরা এককালীন আর্থিক অনুদান পান। আর শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেধাবীদের এককালীন শিক্ষা অনুদান দেওয়া হয়।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফয়সাল আহমেদ বলেন, এ উপজেলায় বসবাসরত ১৪টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কৃষ্টি-কালচার সংরক্ষণে আমরা কাজ করছি। শিগগিরি এসব জাতিগোষ্ঠীর মানুষদের অংশগ্রহণে একটি সাংস্কৃতিক মেলা হবে। বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) পরিচালিত প্রাথমিক স্কুলগুলোয় সাঁওতাল ও অন্যান্য ভাষাভাষী শিক্ষককেরা ক্লাস নিচ্ছেন।
জাতীয় আদিবাসী পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি গণেশ মার্ডি জানান, এখানকার ‘আদিবাসী’ মানুষেরা জীবনমানের ক্ষেত্রে সবদিক দিয়ে পিছিয়ে। অন্যের জমিতে একদম অল্প মজুরিতে কৃষি শ্রমিকের কাজ করে নির্বাহ করতে হয় তাদের। দেশের অন্য প্রান্তের তুলনায় এই মজুরির হার অনেক কম। এদিকে, আদিবাসী পল্লিগুলোতে স্যানিটেশন সংকট রয়েছে। বছরভর সুপেয় পানির সংকট চলছে।
তিনি জানান, গোদাগাড়ী উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে বিভিন্ন গ্রামে ৬০ হাজারের বেশি ‘আদিবাসী’ পরিবারের বসবাস। ‘আদিবাসী’দের গ্রামগুলো থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয় অনেক দূরে হওয়ায় শিশুরা নিয়মিত স্কুল যাচ্ছে না। এ ছাড়া ভাষাগত সংকটের কারণেও শিক্ষার প্রাথমিক স্তরেই ঝরে পড়ছে। এখানকার ‘আদিবাসী’রা বেশিরভাগ সবাই ভূমিহীন। ঘরবাড়ির অবস্থা কারোরই ভালো না। মাথা গোজার যে ঠাঁই রয়েছে; অনেকের তা একেবারে জীর্ণ-শীর্ণ।

.png)