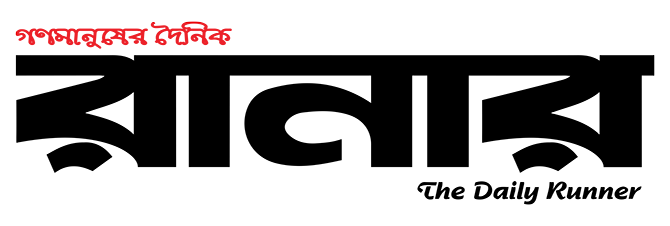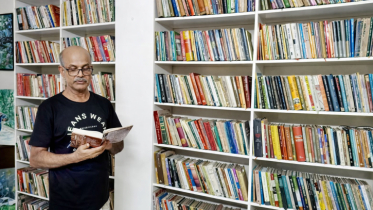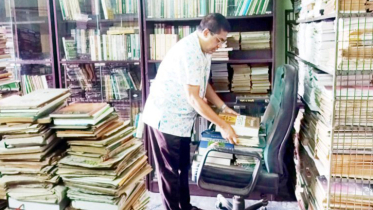কাজী নজরুল ইসলাম (২৪ মে, ১৮৯৯- ২৯ আগস্ট, ১৯৭৬) আমাদের বাংলাদেশের জাতীয় কবি। শুধু বাংলাদেশ নয় ভারতীয় উপমহাদেশ তথা বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে যেসব গুণীজন প্রাত:স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন মানবমুক্তির চিন্তা ও কর্মের মাধ্যমে, তাঁদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম অন্যতম। প্রধানত কবি হিসেবে খ্যাত হলেও বাংলা সাহিত্যের সকল শাখায় তাঁর সিদ্ধহস্ত বিচরণের ব্যাপারটি সর্বজনবিদিত। তবে সবকিছুর উর্ধে তাঁর একটি পরিচয় খুঁজে পাই- তিনি ছিলেন সকল মানুষের আত্মমর্যাদাসম্পন্ন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশভিত্তিক সমাজব্যবস্থা গঠনের উপায় সৃষ্টির এক অনন্য অনুসন্ধানী। নিজে যেমন প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠেছিলেন তেমনি মানব সমাজের সকল সদস্যকেও তাঁর মতই মানবিক মর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়ার ও করার বাণী আজীবন গেঁথে গেছেন কখনো কাব্যে, কখনো গানে, কখনো প্রবন্ধে, আবার কখনো গল্পে-নাটকে। তাঁর মর্মভেদী বিদ্রোহ ছিল সর্বদাই মানুষ, মানবতা ও মানবাত্মার স্বাধীনতার পক্ষে এবং সাম্প্রদায়িকতা, বৈষম্য, অত্যাচার, নিপীড়ন, নির্যাতন, শোষণ ও পরাধীনতার বিপক্ষে। তিনি বিশ্বাস করতেন, সকল মানুষের মানবীয় গুণাবলীসমৃদ্ধ আদর্শিক নৈকট্য ব্যতীত সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপনের পথ সুগম হতে পারে না, কতিপয় সুবিধাভ্গোীর কথা বাদ দিলে সমাজের সকলেই তা আশা করে, কিস্তু অনুশীলন ও সুযোগের অভাবে যা চাপা পড়ে থাকে। শাসকরূপী শোষকগোষ্ঠী এবং তাদের অনুকম্পাপ্রাপ্ত প্রভাবশালী মহলের চাটুকাররা মানুৃষের এই ধারণাকে সর্বদা বাধাগ্রস্ত করে রাখতে চায় আপন স্বার্থ চরিতার্থ করার মানসে। আর এই জায়গায়ই আমরা কবি নজরুলকে দেখি মহাবিদ্রোহীর সমরসজ্জায়- ‘এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতূর্য’।
কাজী নজরুলের মত সুবিশাল ব্যক্তিত্বের আত্মানুসন্ধানের সম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কন করা মোটেও সহজসাধ্য কাজ নয়। আমরা এখানে নজরুলের সুবিখ্যাত প্রবন্ধ ‘আমার পথ’ অনুসরণে সামান্য আলোচনার চেষ্টা করব যাতে তাঁর মানবিকতার উন্নয়নের জয়গান ও সুসভ্য সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার মত মৌলিক অনুসন্ধানের ধারণা লাভ করা যেতে পারে। প্রাসঙ্গিক আরোও কিছু তথ্য আলোচনায় আসতে পারে, যাতে করে আত্মানুসন্ধান ও গণগবেষণার সাথে তাঁর চিন্তার প্রকৃত যোগসূত্র অঙ্কন করা যায়।
২. আলোচ্য প্রবন্ধ থেকে
আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে প্রথমেই‘আমার পথ’ প্রবন্ধের নির্বাচিত কিছু কথা তুলে ধরব (তবে কৌতূহলী পাঠকদের সমীপে অনুরোধ রাখব- নাতিদীর্ঘ এই প্রবন্ধটি যেন পুরোটা পাঠ করে নেন):
‘‘আমার কর্ণধার আমি। আম্য়া পথ দেখাবে আমার সত্য।
যে নিজকে চেনে তার আর কাউকে চিনতে বাকী থাকে না।
নিজকে চিনলে মানুষের মনে আপনা-আপনি এত বড় একটা জোর আসে যে, সে আপন সত্য ছাড়া আর কাউকে কুর্নিশ করে না- অর্থাৎ কেউ তাকে ভয় দেখিয়ে পদানত রাখতে পারে না। এই যে নিজেকে চেনা, আপনার সত্যকে আপনার গুরু, পথপ্রদর্শক কাণ্ডারী বলে জানা, এটা দম্ভ নয় অহঙ্কার নয়, এটা আত্মকে চেনার সহজ স্বীকারোক্তি।
নিজকে চিনলে, নিজের সত্যকেই নিজের কর্ণধার মনে জানলে নিজের শক্তির ওপর অটুট বিশ্বাস আসে। এই স্বাবলম্বন, এই নিজের ওপর অটুট বিশ্বাস করতেই শেখাচ্ছিলেন মহাত্মা গান্ধীজী। কিন্তু আমরা তাঁর কথা বুঝলাম না, ‘আমি আছি’ এই কথা না বলে সবাই বলতে লাগলাম ‘গান্ধীজী আছেন’। এই পরাবলম্বন আমাদের নিষ্ক্রিয় করে ফেললে! একেই বলে সবচেয়ে বড় দাসত্ব। অন্তরে যাদের এত গোলামির ভাব, তারা বাইরের গোলামি থেকে রেহাই পাবে কি করে? আত্মাকে চিনলেই আত্মনির্ভরতা আসে।”
সকল মানুষের মর্যাদাপূর্ণ জীবনের সুবিজ্ঞ চিন্তক নজরুল নিজেকে চেনা বা জানা এবং এর প্রয়োজনীয়তা বা চমৎকার ফলাফল সম্পর্কে তাঁর চিন্তার সামান্য পরিচয় উপস্থাপন করেছেন। এখানে কথা অল্প, কিন্তু তাৎপর্য অপরিসীম।
৩. বিষয়-সংশ্লিষ্ট চিন্তা-ভাবনা
যেকোন প্রকারেই হোক, সকল জ্ঞান যেমন একটি নির্দিষ্ট রেখায় মিলিত হয়ে থাকে, সকল সত্যানুসন্ধানীর ক্ষেত্রেও কথাটি সমভাবে সত্য। আর সত্য ও সত্যার্থীর সার্থকতা সেখানেই। সকল জলধারার চূড়ান্ত গন্তব্য যেমন মহাসাগর, সকল জ্ঞাননালার গন্তব্যও তেমনি সত্যস্বরূপিনী মহাসাগর। তাইতো আমরা দেখি বিশ্বে যারা মানুষের প্রকৃত মুক্তির জন্য চিন্তা ও কর্ম পরিচালনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে কী অপূর্ব সমন্বয়!কিছু কথা এখানে তুলে ধরি:
- Friedrich Engels: With slavery, which attained its fullest development under civilization, came the first great cleavage of society into an exploiting and an exploited class. This cleavage persisted during the whole civilized period. Slavery is the first form of exploitation, the form peculiar to the ancient world; it is succeeded by serfdom in the middle ages, and wage-labor in the more recent period. These are the three great forms of servitude, characteristic of the three great epochs of civilization; open, and in recent times disguised, slavery always accompanies them
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: বাইরে থেকে একটি একটি করে উপকার করে আমরা দু:খের ভার লাঘব করতে পারি নে। এই জন্য উপকার করব না, উপকার ঘটাব, এইটেই আমাদের লক্ষ্য হওয়া চাই। যার অভাব আছে তার অভাব মোচন করে শেষ করতে পারব না, বরঞ্চ বাড়িয়ে তুলব, কিন্তু তার অভাব মোচনের শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে
- Socrates: Know thyself
- লালন সাঁইজী: একবার আপনারে চিনতে পারলে রে যাবে অচেনারে চেনা
- যার আপন খবর আপনার হয় না
- মুখবন্ধ, মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র: মানব পরিবারের সকল সদস্যের সমান ও অবিচ্ছেদ্য অধিকারসমূহ এবং সহজাত মর্যাদার স্বীকৃতিই হচ্ছে বিশ্বে শান্তি, স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচারের ভিত্তি।
বক্তব্যগুলো একটু আলোচনা করা যাক।
প্রথমত, ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস ঐতিহাসিক কাল পরিক্রমায় শোষণ প্রক্রিয়া কীভাবে রূপ বদলের মধ্য দিয়ে সমাজে এর অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে, সে পরিস্থিতির একটি চমৎকার চিত্র তুলে ধরেছেন। দাস থেকে ভূমিদাস অত:পর আধুনিক সভ্যযুগে শিল্পশ্রমিক- বিশেষণে পরিবর্তন এলেও চরিত্র ও ভূমিকায় তেমন কোন পরিবর্তন সূচীত হয়নি। এঙ্গেলস যা দেখাতে চেয়েছেন তা হল- দাসযুগ, সামন্তযুগ, পুঁজিবাদী আমল- সমাজব্যবস্থায় বহু ধরনের পরিবর্তন এসেছে কিন্তু ক্ষমতাবান কর্তৃক ক্ষমতাহীনদেরকে (উৎপাদনযন্ত্রের মালিকপক্ষ কর্তৃক কর্মী বা শ্রমদানকারী পক্ষকে) শোষণ করার যে লোলুপ প্রক্রিয়া, তাতে পরিবর্তন আসেনি, রূপ পাল্টিয়েছে মাত্র। তিনি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, দাসব্যবস্থা সর্বদাই সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অনুসঙ্গী হিসেবে ক্রিয়াশীল ছিল ও আছে। ভবিষ্যতে এটি নির্মূল হয়ে যাবে, এমন কোন উদ্যোগও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।
দ্বিতীয়ত, এহেন পরিস্থিতিতে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর লোকজনকে উজ্জীবিত করে যারা সমাজের উন্নয়নের কাজে ব্রতী হয়েছেন বা হবেন, তাদের কর্তব্য সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। একজন ব্যক্তিকে তার প্রয়োজন বিবেচনা করে আজ চাল, কাল পোষাক, পরশু ওষুধ দিলে উপকার করা হয় বটে, কিন্তু এতে উৎপন্ন হয় পরনির্ভরতার মত এক ভয়ানক ব্যাধি। এর চেয়ে ঐ ব্যক্তিকে জীবিকা নির্বাহের সক্ষমতা সৃষ্টির মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া অধিক উপকারের বিষয়। পল্লীর উন্নয়ন চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ এই সুক্ষè অথচ মূল্যবান বিষয়টিকে ‘উন্নয়ন করা’ ও ‘উন্নয়ন ঘটানো’ হিসেবে দেখেছিলেন।
তৃতীয়ত, মানব সভ্যতার আদি গুরু সক্রেটিসের বক্তব্যের মধ্যে আত্মানুসন্ধানের নিখাদ নির্দেশনা উপলব্ধি করা যায়। আত্মবিশ্লেষণ হলো আত্মানুসন্ধানের প্রথম ধাপ। এই বিশ্লেষণী ক্ষমতা ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। ‘আমি অন্যান্য মানুষের মতই একজন মানুষ’- এই ধারণা পূর্ণাঙ্গভাবে ব্যক্তির বিশ্বাসে বিদ্যমান না হলে সে কোন শুভ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে না।
চতুর্থত, বাংলার বাউল-সাধক ও সমাজ-দার্শনিক লালন সাঁইজীর কথাগুলো সক্রেটিসের কথার সমার্থবোধক কিন্তু বিশ্লেষণমূলক। তিনি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত শক্তি রয়েছে, সেটি উদ্ঘাটিত করার পরামর্শ দিয়েছেন। এই শক্তিই হচ্ছে মানুষেল আসল শক্তি, যার সার্থক সম্মিলন গোটা সমাজকে পরিবর্তন করে দিতে পারে।
পঞ্চমত, জাতিসঙ্ঘ ১৯৪৮ইং সনে ‘মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র’ প্রণয়ন করে মানুষের মানবিক মর্যাদা ও সম-অধিকারের বিষয়টিতে দান করেছে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো। অর্থাৎ, মানুষের মর্যাদা ও অধিকারের বিষয়টিকে খণ্ডিতভাবে উপস্থাপন করার কোন সুযোগ নেই; মানৃুষের পরিচয়কে রাজনীতি, অর্থনীতি, ভূগোল, ইতিহাস, কূটনীতি কিংবা ধর্মনীতিতে আবদ্ধ করার কোন ক্ষমতা কারো নেই।
৪. আত্মানুসন্ধান
আত্মানুসন্ধান হলো নিজেকে জানা ও চেনার প্রচেষ্টা- নিজের মধ্যে কি কি শক্তি বিদ্যমান রয়েছে এবং কি কি ঘাটতি রয়েছে সেসবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা। নিজেকে বস্তুনিষ্টভাবে জানলেই কেবল ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কাঙ্খিত পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে পারে। যেকোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সমাজের এহেন অনুসন্ধানের প্রাথমিক ও আসল উদ্দেশ্য হলো আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করা- নিজের ওপর নিজের আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপনের উপযুক্ততা বা যোগ্যতা সৃষ্টি করা।
আত্মনির্ভরশীলতা ব্যক্তি, গোষ্ঠী তথা জাতির মৌল চালিকাশক্তি। আত্মনির্ভরশীলতা অধিকার, মর্যাদা, উন্নয়ন, অগ্রগতি এমনকি গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থারও অলঙ্ঘ্যনীয় পূর্বশর্ত ও রক্ষাকবচ। ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বাভাবিক জীবন যাপনের প্রাত্যহিক চাহিদা পূরণে যেখানে পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকে, সেখানে কোন আদর্শই প্রকৃতার্থে সফল হয়ে উঠতে পারে না। বলা আবশ্যক যে, কেবল অন্ন, বস্ত্র, ব্সাস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বিনোদনের ব্যবস্থা থাকলেই আত্মনির্ভরশীলতা নিশ্চিত হতে পারে না; বরং এর জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন হচ্ছে যেকোন বিষয়ে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সক্ষমতার নিশ্চয়তা। সক্ষমতাভিত্তিক এই স্বাধীনতা ব্যতীত অন্যান্য সব কিছুর যোগান নিরর্থক হয়ে পড়ে। এই উপলব্ধির স্ফূরণ ও বাস্তবায়নের পথে আত্মানুসন্ধান কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে যে, আত্মানুসন্ধান বা নিজেকে জানার প্রচেষ্টা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর চিন্তা ও কর্মে পরিবর্তন এনে একটা সামাজিক আন্দোলন হিসেবে দাঁড়িয়ে যেতে পারে, যদি যথাযথ পদ্ধতিতে একে পরিচালনা করা হয়।
এই অনুসন্ধানের প্রক্রিয়াটি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে দীর্ঘদিন ধরে শোষণ-নিপীড়নের মধ্যে অবস্থান করার ফলে; কারণ, ক্ষমতার অপব্যবহার করে স্বার্থান্বেষী মহল সর্বদাই অপেক্ষাকৃত দুর্বল গোষ্ঠীগুলোকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টায় লিপ্ত হয়। যদিওঅনুশীলন বা চর্চার অভাবে জ্ঞান সুপ্ত বা নির্জীব হয়ে পড়ে তথাপি নিয়মসিদ্ধ চর্চার মাধ্যমে তাকে সজীবতা দান করা সম্ভব। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, সকল বীজেই প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু যথাস্থানে বীজকে স্থাপন না করলে সে বীজ থেকে প্রাণের সঞ্চার ঘটতে পারে না। কৃষক উৎপাদিত ফসলের নির্দিষ্ট অংশ বীজরূপে সংরক্ষণ ও পরিচর্যা করে থাকেন এবং নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে বীজের বুনন বা রোপণ সম্পন্ন করেন এবং কেবল তখনই প্রাণের সূচনা সুনিশ্চিত হয়ে পুনরায় ফসল উৎপাদনের নিয়োজিত হয়। ঠিক এভাবেই রুদ্ধ বা সুপ্ত জ্ঞানকে জাগিয়ে তোলা যায়। গণগবেষণার অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক মো: আনিসুর রহমান ‘মগজ থেকে মরচে সরানো’ বলতে এ বিষয়টিই মূলত বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। তাঁর কথায়.‘‘উন্নয়ন অর্থ গণজীবনের গর্বিত আত্মবিকাশ, মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিকুল অবস্থার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়া;.. .. মানুষ নিজের যা আছে তাই নিয়ে গর্বের সঙ্গে এগিয়ে যায় অপরের করুণামিশ্রিত দান প্রত্যাখ্যান করে. তার বিত্ত যত কমই হোক সে দরিদ্র নয়, তার কোন দারিদ্র্যের সমস্যা নেই, এই সমস্যা যে তাকে বাইরে থেকে দেখে এবং তার চরিত্রের দীপ্তি দেখতে পায় না, তার।.. .. মানুষের মধ্যে এই দীপ্তি অনেক সময় পারিপার্শ্বিক সংস্কৃতিব আড়ালে লুকিয়ে থাকে, কিন্তু তাকে উদ্ভাসিত করা যায় এবং এই কাজটিই উন্নয়ন প্রচেষ্টার নেতৃত্বের কাজ।” আত্মানুসন্ধান প্রত্যয়টি উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে এ এক চমৎকার বক্তব্য।
৫. গণগবেষণা
গণগবেষণা মানে একটি অনুভূতি। কী সে অনুভূতি?
এ অনুভূতি সকলকে নিয়ে এগিয়ে চলার অনুভূতি, যা ব্যক্তির ভেতর থেকে উৎসারিত হয়ে গোটা জনগোষ্ঠীতে বিস্তার লাভ করে। বস্তুত সামাজিক উন্নয়ন কোন একজনের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না, প্রয়োজন সকলের অংশগ্রহণ। সকলের চিন্তা ও কর্ম একত্রিত করে সম্মুখে এগিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিলে তা সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনে বহু মানুষের সমন্বয়ে আয়োজিত ও পরিচালিত আালোচনা ও কর্মের উদ্যোগই গণগবেষণা। যখন অনেক মানুষ স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে একত্রিত হয়ে আলোচনা বা পর্যালোচনা করে কোন একটি লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করে, তখন তা গণগবেষণার রূপ ধারণ করে। গণগবেষণায় সমষ্টিগত আলোচনা বা অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ফলে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের চোখ, কান ও মস্তিষ্ক উন্মুক্ত হয়ে যায়, তারা পরিচিত হতে থাকে এক ভিন্ন জগতের সাথে। তাই তথ্যসমৃদ্ধ হওয়া ও সৃজনশীল মানসিকতা অর্জন করার অনন্য বাহন হলো গণগবেষণা।
গণগবেষণা প্রত্যয়টিকে সংজ্ঞায়িত করা বেশ জটিল বিষয়। কেননা, এর কর্মপরিধি পরিমাপ করার মত নয়। বলা যায়, যেখানে সমস্যা সেখানেই গণগবেষণা। তাই মহলবিশেষের দারিদ্র্য বিমোচনের পন্থা হিসেবে গণগবেষণাকে সীমিত করার চেষ্টার পরিবর্তে সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে একে বিবেচনা করাই শ্রেয়তর ও অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। এরই সাক্ষ্য পাওয়া যায় গণগবেষণার নিরন্তর অনুসন্ধানী ড. শামসুল বারির বর্ণনায়। তিনি বলেন, “গণগবেষণা হচ্ছে অনেক মানুষের একত্র হয়ে কোন বিষয় বা পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে সত্যের অনুসন্ধান করা এবং এগিয়ে যাবার পথ নির্ণয় করে উদ্যোগ নেওয়া। গণগবেষণার মাধ্যমে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে জনগণ সমষ্টি বা গোষ্ঠী হিসেবে তাদের জীবনযাত্রা, তাদের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ, তাদের দারিদ্র্যের কারণ ও তা থেকে পরিত্রাণের পথ ইত্যাদি বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে, দারিদ্র্য থেকে উত্তরণের জন্য তাদের নিজেদেরই কি কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ, সে ব্যাপারে গোষ্ঠীবদ্ধ ও একক সিদ্ধান্ত নেয়।” এ থেকে আমরা পরিস্কার বুঝতে পারি যে, সমষ্টির উদ্যোগে ও সমষ্টির কল্যাণে কোন বিষয় বা পরিস্থিতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে সত্য উদ্ঘাটন করে তা বাস্তবায়নে সমষ্টির প্রচেষ্টার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া হলো গণগবেষণা। দারিদ্র্য প্রত্যয়টি এখানে বিজড়িত হতে পারে শুধু মনোজাগতিক কারণে। কেননা, মানসিক দারিদ্র্যই সকল প্রকার দারিদ্র্য বা সমস্যার সূতিকাগার। মনো-সামাজিক দারিদ্র্যের কিছু প্রকাশ রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে অবৈজ্ঞানিক ভেদবৈষম্য, অমানবিক হানাহানি, প্রশাসনিক অস্থিতিশীলতা, অনৈক্য, স্বার্থান্ধতা, পরমতে অসহিষ্ণুতা, হীনমন্যতা, সমস্যার বিশ্লেষণে অনীহা সহ বহুমুখী সাম্প্রদায়িকতা ও সীমাবদ্ধতা। যার ফলে সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না।সকলের চিন্তা ও কর্মকে একত্রিত করতে না পারাটাকেও নি:সন্দেহে এই তালিকায় যুক্ত করা যায়।
মানব জীবনে সমস্যার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। তাই স্বভাবতই গণগবেষণা হচ্ছে এমন একটি চলমান প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সম্মিলিত চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করে কোন সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সমস্যার কারণ, ধরণ, ব্যাপ্তি প্রভৃতির ব্যাখ্যা-বিশ্লে¬ষণ, সমস্যা নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়ন-পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, প্রতিফলন মূল্যায়ন প্রভৃতি কর্ম পরিচালনা করে থাকে। ফলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যক্তি-গোষ্ঠী সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত হয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মবিশ্বাসের পথ ধরে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের পথে এগিয়ে যায়।
৬. কাজী নজরুলের চিন্তার সাথে প্রত্যয়গুলোর সাযুজ্য
আলোচিত বিষয়গুলোর সাথে কাজী রজরুলের চিন্তার কতটুকু সাযুজ্য রয়েছে, তা বোধ হয় সবিস্তারে উপস্থাপন করার কোন প্রয়োজন নেই। তবে অতি সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায়, আলোচিত প্রতিটি বাক্যের মধ্যেই মানবদরদী এই ব্যক্তিত্বের স্বল্প ও সুচিন্তিত কথার স্পর্শ রয়েছে। নিজেন ওপর আস্থা স্থাপনের বিষয়টিকে তিনি অত্যন্ত গভীরগুরুত্ব সহকারে দেখেছেন; তিনি মহাত্মা গান্ধীর ওপর আস্থা স্থাপনের পরিবর্তে ব্যক্তিকে নিজের ওপর আস্থা স্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন। সকল জনগোষ্ঠীর মধ্যেই এগিয়ে চলার বা পরিবর্তনের জ্ঞান রয়েছে- গণগবেষণার অন্যতম এই মূলনীতিটিকে কাজী নজরুল পেশাদার গবেষকেরঅন্তর্দৃষ্টি নিয়ে চমৎকারভাবে উপলব্ধি করেছেন:
তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে দেখ নিজ প্রাণ।
গণগবেষণার মাধ্যমে আত্মানুসন্ধানের যে কথাগুলো আমরা বার বার উচ্চারণ করে থাকি, কাজী নজরুল মাত্র দু’টি চরণে তা তুলে ধরেছেন।
ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থার যে চিত্র অঙ্কন করেছেন, কাজী নজরুলের অনুসন্ধান এর চেয়ে ভিন্নতর নয়। মো: ্আনিসুর রহমানও‘পারিপার্শ্বিক সংস্কৃতি’ বলতে এই একই সমাজব্যবস্থাকে বুঝিয়েছেন। নজরুল স্বার্থান্বেষী ক্ষমতাধরদের সম্পর্কে বহু ব্যাঙ্গাত্মক বিশেষণ ব্যবহার করেন এবং পরিশেষে দেশের চিরবঞ্চিত, অবহেলিত ও নি:স্ব চাষীদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে জেগে ওঠার মর্মস্পর্শী আহ্বান জানান:
ওঠরে চাষী জগদ্বাসী ধররে ক’ষে লাঙ্গল .. ..
আজ জাগরে কিষাণ! সব তো গেছে কিসের বা আর ভয়?
এই ক্ষুধার জোরেই করব এবার সুধার জগৎ জয়।
ঐ বিশ্বজয়ী দস্যুরাজার হয়কে করব নয়,
ওরে দেখবে এবার সভ্য জগৎ চাষার কত বল।
মানুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টিকে নজরুল অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখেছেন। তিনি সর্বদা চেয়েছিলেন সবার জন্য বাসযোগ্য একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্ব, যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, ধনী, নির্ধন, রাজা, প্রজা নির্বিশেষে মানবিক মর্যাদার বিচারে কোন ভেদাভেদ থাকবে না, মানবজাতির সকল সদস্য একই মানদণ্ডে বিবেচিত হবে এবং সকলেই যার যার সামাজিক ব্যবস্থার অধীনে ন্যায্যভাবে প্রাপ্তব্য উপাদান বাধাহীনভাবে উপভোগ করবে, আবার দেয় উপাদানগুলোও অকৃপণভাবে দান করবে। মানুষে মানুষে এই পারস্পরিকতা না থাকলে সুষ্টু সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। তিনি নির্মোহভাবে চেয়েছিলেন সকলে মিলে দেশের সেবা করার; যার যা সাধ্য রয়েছে, সেগুলোকে একত্রিত করে তবেই এগিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে তিনি অনুপ্রাণিত করেন। নজরুলের সমাজমানসে অবহেলিত, নিপীড়িত, শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের মুক্তির বার্তা অতিশয় সুস্পষ্ঠভাবে ফুটে উঠেছে, যা তাঁর বহু রচনায় বিবৃত হয়েছে। সকল বাধা ব্যবধান চিরতরে দূর করে তিনি যে সাম্যের সমাজ সর্বান্তকরণে কামনা করেছিলেন, তার জন্য সকল মানবাত্মার প্রকৃত মর্যাদা ও স্বাধীনতার কথা বার বার বলে গিয়েছেন। নিজেকে চেনা বলতে তিনি মূলত এই অসামান্য কথাটিই বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি মানুষের তথা মানবাত্মার সর্বোচ্চ মিলনের আশায় আজীবন কলমযুদ্ধ করেছেন। এখানেই দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে এঙ্গেলস, সক্রেটিস, লালন, রবীন্দ্রনাথ ও জাতিসঙ্ঘ-ঘোষিত মানবাধিকবারের সারবত্তার সাথে নজরুলের চিন্তার সার্থক সাযুজ্য। তাঁর কথা:
গাহি সাম্যের গান
যেখানে এসে এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান।
মানুষে মানুষে কাল্পনিক, অগণতান্ত্রিক ও অমানবিক স্তরবিন্যাসের মূল উৎপাটনের লক্ষ্যেই গণগবেষণা পরিচালিত হয়, যেখানে বঞ্চিতজন নিজেরাই গবেষকের আসনে অধিষ্ঠিত হন, বাইরের কেউ এখানে পরিচালনা বা নেতৃত্বে আসীন হতে পারেন না, বড়জোর তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করতে পারেন।
৭. উপসংহার
কাজী নজরুল গণগবেষণা শব্দটি ব্যবহার করেননি, করার কথাও নয়। কেননা, তাঁর জীবদ্দশায় শব্দটির উদ্ভব ঘটেনি; তাঁর মৃত্যুর পরের দশকে গণগবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো রচিত হয়। কিন্তু শব্দটির ক্রিয়াশীলতা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি তিনি তুলে ধরেছেন ঠিকই। এর আসল কারণ হল, মানুষের এগিয়ে চলার পাথেয় হিসেবে সমষ্টিগত চেতনা সৃষ্টির উদ্যোগ আদি যুগ থেকেই বিদ্যমান ছিল, যার পেছনে ছিল কতিপয় মহান ব্যক্তিত্বের অখণ্ড মানবতামুখিন চিন্তা ও কর্ম। কাজী নজরুল ইসলাম সে মহান হিতৈষী গোষ্ঠীরএকজন গর্বিত সদস্য, যিনি ‘অসির চেয়ে মসী বড়’- এই আত্মোপলব্ধি থেকে আজীবন কলম চালিয়েছেন মানবিকতার পক্ষে, অনুসন্ধান পরিচালনা করেছেন মানবতার মুক্তির টেকসই উপায় সৃষ্টির লক্ষ্যে।সকল প্রকার অনুসন্ধান বা গবেষণার মূল উদ্দেশ্য সত্য উদ্ঘাটন করা অথবা প্রচলিত সত্যকে যাচাই করে দেখা। বৃহত্তর গবেষণা জগতের সদস্য হিসেবে গণগবেষণাও একই উদ্দেশ্যে চালিত। সত্যব্রত কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যাংশ দিয়েই আলোচনার সমাপনী টানতে চাই:
সত্য যদি হয় ধ্রুব তোর,
কর্মে যদি না রয় ছল,
ধর্ম-দুগ্ধে না রয় জল,
সত্যের জয় হবেই হবে,
আজ নয় কাল মিলবে ফল
.. ..
জাতের চেয়ে মানুষ সত্য,
অধিক সত্য প্রাণের টান,
প্রাণ-ঘরে সব এক সমান।
কাজী নজরুলের প্রত্যাশিত ‘প্রাণ-ঘরে’ সকল মানব সন্তানের সম সম্মিলন সুনিশ্চিত হোক,এ লক্ষ্য অর্জনের জন্যই প্রয়োজন আত্মানুসন্ধান, প্রয়োজন গণগবেষণার সুষ্টু পরিচালনা।
লেখক:
বাবুল চন্দ্র সূত্রধর
মানবাধিকারকর্মী ও গবেষক
মোবাইল: ০১৭১২৬৪৯৬৪১

.png)